বাংলা ভাষায় চিকিৎসা শিক্ষা – অধ্যাপক ডা. এম আমজাদ হোসেন
- আপডেট সময় : মঙ্গলবার, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪
- ১১৭ বার পঠিত

অতি সম্প্রতি হাইকোর্ট একটি মামলার রায় বাংলায় লিখে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আশা করি, এই শুভ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আমি অধীর আগ্রহী, একদিন আমাদের চিকিৎসাশিক্ষাও বাংলা ভাষায় হবে।
পৃথিবী জুড়েই জনগণের মাঝে উচ্চশিক্ষার প্রসার হয়েছে, ইংল্যান্ড কিংবা জাপান কিংবা চীন, কেউই ব্যতিক্রম নয়। বরং, যখন সাধারণতম পরিবারের, প্রান্তিক, গ্রামীণ ও মফস্বলের নারী ও পুরুষ শিশুরাও যথাযথ শিক্ষার সুযোগ পায়, তখনই সত্যিকারের মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান পেতে থাকে।
আমি বরাবরই বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার পক্ষপাতী। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, উচ্চশিক্ষাও। চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াশোনা তো বেশ জটিল। একটা উদাহরণ দিলই বোঝা যাবে, লিখিত পরীক্ষা খুব ভালো দিয়ে অনেকেই মৌখিক পরীক্ষায় উত্তর দিতে দিয়ে তোতলায়। অর্থাৎ, জানা জিনিস অন্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন… এই কথাটা আমি লিখেছিও বহু জায়গায়—তখন পরীক্ষক মনে করেন এ তো কিছু জানেই না…
বাংলায় চিকিৎসাশাস্ত্রের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার শিক্ষা বিষয়ে একটা বড় আপত্তি করা হয় বিদেশীদের সাথে যোগাযোগে ঝামেলা হবে বলে। একই আপত্তি প্রকৌশল বা অন্য সব বিদ্যার জন্যও প্রযোজ্য। এরা কখনো বিবেচনা করে দেখেন না যে, বাঙালী একজন চিকিৎসক কদাচিৎ বিদেশীদের মুখোমুখি হন, তার চাইতে অনেক বেশি বিদেশী রোগী দেখেন থাই চিকিৎসক। অন্যদিকে, মাতৃভাষায় পড়াবার কারণে যদি পাঠদানের মান ভালো হয়, সেটাই অনেক বড় অর্জন হবে। একইসাথে, প্রয়োজন হবে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত একটা জাতীয় অনুবাদ কেন্দ্রের, যারা প্রতিনিয়ত সারা পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণা সাময়িকীগুলো থেকে লেখা অনুবাদ করতে থাকবেন এবং সেগুলো পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হতে থাকবে। চিকিৎসকদের অনেকেই ইংরেজি, জাপানী, জার্মান, কোরীয় বা নানান বিদেশী ভাষা শিখবেন, সেখান থেকে জ্ঞান সম্পদ বাংলাতে নিয়ে আসবেন। তারা যোগসূত্রের কাজটি করবেন। এবং সারা দুনিয়ার অভিজ্ঞতাই বলে, এভাবে কাজটি সম্পাদনা করলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়, বিদেশী ভাষাকে তখন আগ্রহীদের জন্য আলাদা একটা বিষয় হিসেবে শেখানো হয়, কিন্তু কিছুতেই বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয় না। অর্থাৎ মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চাকে যারা অন্য ভাষা ‘নিষিদ্ধ’ বা ‘চর্চা নিরুৎসাহিত’ করার তুল্য বলে ভাবেন বা প্রচার করেন, তারা হয় বিষয়টা বোঝেন না, অথবা অপপ্রচার করে থাকেন।
আশার কথা হলো, বাংলাদেশের জনগণের ভিন্ন একটা বাস্তবতা ইংরেজি ভিত্তিক এই এলিট স্বার্থকে অনেকখানি ক্ষয়িষ্ণু করেছে। সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও শিক্ষার বিস্তার চিকিৎসা শিক্ষাকে এখন আর উচ্চবিত্তের মাঝে সীমায়িত রাখছে না।
“বাংলাদেশে যেখানে সর্বত্র শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয় না, সেখানে চিকিৎসাশিক্ষার মতো টেকনিক্যাল ও জটিল বিষয় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব কতটুকু বাস্তবসম্মত? যাঁরা ভাবছেন এটি অলীক চিন্তা, তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ইতিমধ্যেই আমাদের মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে লেকচার ক্লাসের অন্তত অর্ধেক বাংলায় করা হয়; ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বেশির ভাগ বাংলাতেই হয়ে থাকে। এ রকমটি অনিবার্য, কেননা বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে ও বুঝে নিতে মাতৃভাষায় আলাপচারিতা করতেই হয়। কোনো কিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে কথা বলতে গেলে মায়ের ভাষা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এসে যাবে। অন্তত হওয়া উচিত। আর প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো প্রায় পুরোটাই বাংলা ভাষায় করা হয়ে থাকে।”
কিন্তু, বাজারে একটা চালু প্রচার আছে যে, শিক্ষার এই ব্যাপক প্রচলনের কারণে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে! এই প্রচারণার মাঝেও সেই এলিট ভূতটিই কার্যকর। পৃথিবী জুড়েই জনগণের মাঝে উচ্চশিক্ষার প্রসার হয়েছে, ইংল্যান্ড কিংবা জাপান কিংবা চীন, কেউই ব্যতিক্রম নয়। বরং, যখন সাধারণতম পরিবারের, প্রান্তিক, গ্রামীণ ও মফস্বলের নারী ও পুরুষ শিশুরাও যথাযথ শিক্ষার সুযোগ পায়, তখনই সত্যিকারের মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান পেতে থাকে। শিক্ষার মানের ভালো-মন্দ নির্ভর করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর, বিষয়কে বোঝাবার মত যোগ্য শিক্ষক ও উপকরণাদির ওপর। শিক্ষার্থীর ভাষা কিংবা আর্থিক যোগ্যতার ওপর না।
ফলে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা শিক্ষা [এমনিভাবে আরও সকল উচ্চশিক্ষা] প্রদানে বাধা কারা? কারা এটাকে ধীরগতির করে ফেলছে? এবং কিভাবে উত্তরণ হবে? এই দুটো প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু সংক্ষেপে বলা যায়:
ক. বাংলায় চিকিৎসা শিক্ষা দেয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে বাঙালী ক্ষুদ্রমনা এলিটের কায়েমী স্বার্থ, এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব। বাংলাতে চিকিৎসা শিক্ষা দেয়ার পথে প্রধান চাহিদা তৈরি করছে অ-এলিট জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সাথে যুক্ততা।
খ. বাংলায় চিকিৎসা শিক্ষা দেয়ার জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যপুস্তকের অগ্রাধিকার নির্ণয়, বাংলায় তা প্রণয়ন, এবং সেটার মান যাচাই ও সম্পাদনার বন্দোবস্ত করা হলে- বাংলায় এটা ঘটবে দ্রুত এবং যথাযথ গুনগত ভিত্তি অটুট রেখেই।
শেষতঃ, এটুকু বলা যায়, ভাষার চাহিদা না থাকায় নাইজেরিয়ার ইগবো ভাষাটি [যে ভাষার মানুষ ছিলেন চিনুয়া আচেবে] মত সংখ্যা বাড়তে থাকা জনগোষ্ঠীর ভাষাও আমাদের চোখের সামনেই বিলুপ্ত হতে চলেছে [কিন্তু দেশটির অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজিতেই অনুত্তীর্ণ হয়, মাতৃভাষা হারিয়েও]। অন্যদিকে বাংলা ভাষার আশার দিকটি হলো এর পরবাসী মনের অধিকারী এলিট অংশের সকল অনীহা, অনিচ্ছা এমনকি কখনো কখনো বদদোয়া সত্ত্বেও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর পদচারণা নিত্যই বাড়ছে, বাংলা ভাষার চাহিদাও বাড়ছে। বাংলায় চিকিৎসা শিক্ষা [আর সকল উচ্চশিক্ষা সমেত] আজ কিংবা কাল দেয়া বাস্তবায়ন হবেই। কিন্তু সেটা কি এইরকম অবক্ষয়ী প্রক্রিয়ায়, নাকি সুসমন্বিত একটা পরিকল্পনা মাফিক, সেটাই প্রশ্ন। রবি ঠাকুর বলতেন, সভ্যতা মানে প্রস্তুতি; অর্থাৎ পরিকল্পনা। বাংলাদেশের পরবাসী মনের আমলা/শাসক/নীতিনির্ধারকগণ বরং তাদের সকল প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা দিয়ে যা অবশ্যসম্ভাবীরূপে ঘটবেই, তাকে বিলম্বিত করার চেষ্টাটিই প্রাণপণে করে যাচ্ছেন।




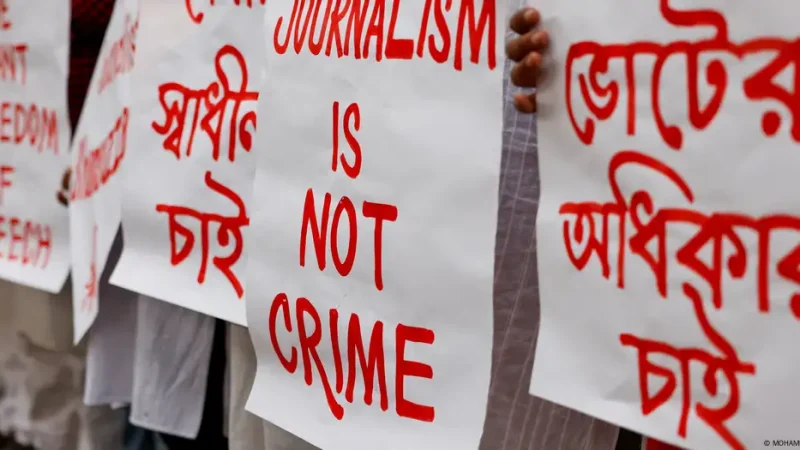
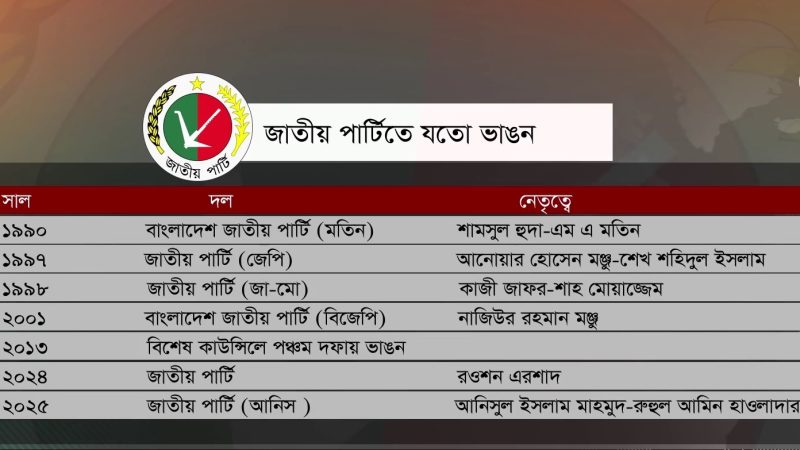




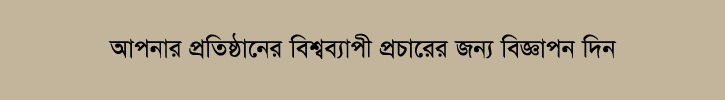








Leave a Reply